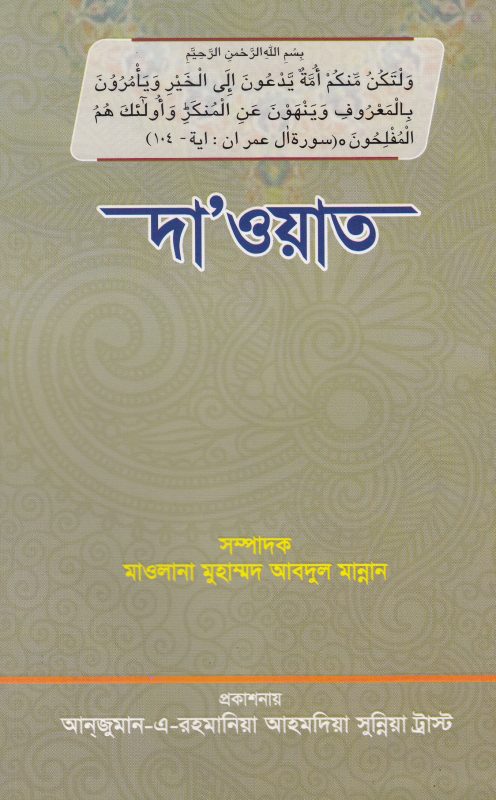
ইসলামি সংস্কৃতির প্রকৃতি, তাৎপর্য ও এর পরিধি
অ্যাডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার
‘সংস্কৃতি’ বিমূর্ত বিষয়। এর কোনো বস্তুগত স্বরূপ নেই। দেখা যায় না, ছোঁয়া যায়না- এমন কিছু বিধায় একে শুধু অনুভব করা যায়। বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার বিষয় এটি। সংস্কৃতি সম্পর্কে একেকজন একেকভাবে ধারনা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন জনের ধারনার আলোকে ও বিশ্লেষণে এর একটি সাধারণ জ্ঞান বা ধারণা আমাদের দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে। এরই মাপকাঠিতে সংস্কৃতি বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছে এ পর্যন্ত।
বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি
ইংরেজি ঈঁষঃঁৎব শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাঙলায় ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি পরিচিত। এর আভিধানিক অর্থ-শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। সম্-কৃ (করা)+ ক্তি-এ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত পরিশ্রুত, নির্মলীকৃত শোধিত ধরনের অনুভবসমূহ। ফলে উৎকর্ষময় বা পরিশ্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতির সার কথা-এ উক্তি মূলানুগ।[নরেন বিশ্বাস, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশর সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯] ড. আহমদ শরীফ বলেন, সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গলের প্রতি মানুষের যে প্রবণতা, মানুষ সচেতনভাবে চেষ্টা দ্বারা যে সুন্দর চেতনা, কল্যাণকর বুদ্ধি ও সুশোভিত জগৎময় দৃষ্টি অর্জন করতে চায়- তাকেই হয়তো তার সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়। সংস্কৃতি হল মানুষের অর্জিত আচরণ, পরিশুদ্ধ জীবন-চেতনা। জীবিকা-সম্পৃক্ত পরিবেষ্টনী প্রসূত হলেও প্রজ্ঞা ও বোধিসম্পন্ন ব্যক্তি চিত্তেই এর উদ্ভব এবং বিকাশ। ব্যক্তি থেকে ক্রমে সমাজে এবং সমাজ থেকে বিশ্বে তা হয় ব্যাপ্ত। চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর, শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। [তাজুল ইসলাম হাশেমী, ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সুকান্ত একাডেমী, পৃ. ৫৫]
মোতাহার হোসেন চৌধুরী’র মতে, সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সহায়তায়। এই নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলার নাম কালচার। তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের সাধনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না ঘটলে কালচার্ড হওয়া যায়না। তিনি বলেন, সত্যকে ভালোবাসো, সৌন্দর্যকে ভালোবাসো, ভালোবাসাকে ভালোবাসো, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসো, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসো-এরি নাম সংস্কৃতি। তাঁর মতে সংস্কৃতির অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ।
তিনি মনে করেন, অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা এ তো সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানে জীবনের ঠধষঁবং সম্বন্ধে ধারনা। তিনি বলেন, সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ-নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা। বন্দুকের নলেই যারা জীবনের একমাত্র সার্থকতা খুঁজে পান তারা কালচার্ড নন। তাঁর মতে, কালচার্ড লোকেরা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে। [সূত্র.মোতাহার হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতির কথা] কীভাবে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল ফজল তাঁর ‘সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবন’ গ্রন্থে বলেন, ‘কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিকের সৃষ্টিকে হজম করেই সংস্কৃতিকে করা যায় আয়ত্ব ও একমাত্র এভাবেই হওয়া যায় সংস্কৃতিবান। কতিপয় সৃষ্ট বিষয় যখন অনেকের উপভোগের ব্যাপার হয়, অতীত ও বর্তমানের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলো যখন মানুষ সাগ্রহে গ্রহণ করে ও তার উপযুক্ত মূল্য দেয়, তখনই সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। [সূত্র. আসাদ বিন হাফিজ, ইসলামী সংস্কৃতি, পৃ.২৩]
বদরুদ্দিন ওমরের মতে, ‘জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তাঁর শোকতাপ, আনন্দ বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য, ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সব কিছুরই মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।
আবুল মনসুর আহমদ তাঁর ‘বাংলাদেশের কালচার’ গ্রন্থে বলেন, ‘‘কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোন এক ব্যাপারে একটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার বিধি মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টর, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে এ ব্যাপারে ওই মানব গোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে।’’
গোপাল হালদার ‘সংস্কৃতির রূপান্তর’ গ্রন্থে বলেন, সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবন যাত্রার আর্থিক ও সামাজিকরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিস্ক্রিয়া আর নানা শিল্প সৃষ্টি, সমস্ত চারু ও কারু কলা-এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ।’
পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি
ডিউই বলেন, CULTURE MEANS AT LEAST SOMETHING CULTIVATED, SOMETHING REPENED. IT IS OPPOSED TO THE RAW AND CRUDE. অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অমার্জিত ও অপরিণতের পরিপন্থী।
টেইলর বলেন,CULTURE IS THE COMPLEX-WHOLE WHICH INCLUDES KNOWLEDGE, BELIEF, ART, MORAL LAW, CUSTOM AND ANY OTHER CAPABILITES AND HABITS ACQUIRED BY MEN AS A MEMBER OF SOCIETY. অর্থাৎ সংস্কৃতি হলো সমাজের মানুষের অর্জিত জ্ঞান, বিশ্বাস শিল্পকলা, নেতিক আইন, প্রথা, সংস্কার ও অন্যান্য বিষয়ে জটিল সমাবেশ। [আসাদ বিন হাফিয, ইসলামী সংস্কৃতি, পৃ.২৪]
রাশিয়ান চিন্তাবিদ ট.ভি.ডি রবার্টির মতে, সংস্কৃতি হলো অনুমানগত ও ফলিত সব চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমষ্টি। গ্রাহাম ওয়ালেসের মতে, সংস্কৃতি হলো, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও বস্তুর সমষ্টি, এক কথায় সামাজিক ঐক্য। আর, বি. মালিনওস্কির মতে, সংস্কৃতি হলো, মানুষের ক্রমবর্ধমান সৃষ্টির সমষ্টি। রবার্ট রেডফিল্ড বলেছেন, সংস্কৃতি হলো সমগ্রভাবে ‘সমঝোতাসমূহের অংশ।’ র্যাডক্লিফ ব্রাউনের মতে, সংস্কৃতি মূলতই একটি ‘নিয়ম কানুনের ধারা’।
উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বুলবুল ওসমান তাঁর ‘সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব’ বইয়ে বলেন, ‘মানুষের সমগ্র সৃষ্টির বিভিন্ন নাম, যেমন- ভাষা, কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন, রাষ্ট্র, নৈতিকতা, ধর্ম-তাছাড়া সমগ্র যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক দ্রব্যাদি এবং এই সমস্ত দ্রব্য নির্মাণের সমস্ত বিদ্যা, ঐতিহ্য, রীতি-প্রথা, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান-এর সবই পড়ে সংস্কৃতির আওতায়। সংস্কৃতি ধারণাকে উপরোক্ত অভিমতসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় যে, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক-বিস্তৃত ব্যাপার। মানুষের সামগ্রিক অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য জীবনাচারের অপর নাম সংস্কৃতি। মূল্যবোধ এর অপরিহার্য পূর্বশর্ত বিধায় বিশ্বাসই এর মূলভিত্তি। মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করতে গিয়ে তার বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আওতায় যা যা করে তাই সংস্কৃতি। মানুষের কাজ-আচরণ শুধু নয় তার ব্যবহারের জিনিষ-পত্রকেও সংস্কৃতির আওতায় আনা হয়েছে। মানুষের যাবতীয় সৃষ্টি যেমন সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আইন-কানুন ইত্যাদি সবকিছু। সুতরাং সংস্কৃতি এতো ব্যাপক একটি ব্যাপার যে, একে মানুষের সামগ্রিক পরিশীলিত কর্মকান্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে, সমগ্র পর্যায়ে।
অথচ আজ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতি শব্দটি উচ্চারিত হলেই আমাদের মানসপটে এক সংকীর্ণ কর্মকান্ডের কথা বার বার ভেসে আসে। সংস্কৃতিকর্মী বলতে আমরা আজকাল বুঝি বিনোদন কর্মীদের। যারা নাটক-থিয়েটার করে। গান গায়-নাচে। ভাষাতত্ত্বের ভাষায়, এটা সংস্কৃতি (Culture) অভিধাটির অর্থ সংকোচনের এক সাম্প্রতিক উদাহরণ বটে। বাংলাদেশে এ শব্দটির ব্যাপকতা ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে এবং সংকীর্ণ একটি পরিমন্ডলের সাথে যুক্ত থাকছে মাত্র। নাটক-গান-নাচ ইত্যাদি বিনোদনধর্মী কাজগুলো এক শ্রেণির মানুষের সামগ্রিক সংস্কৃতির একটি ক্ষুদ্র অঙ্গ মাত্র। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংস্কৃতি কর্মী নিঃসন্দেহে। তবে, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের একটি সীমিত মন্ডলের কর্মী এরা। রাজনৈতিক কর্মীরাও সাংস্কৃতিক কর্মী; বরং এদের সীমানা তুলনামূলকভাবে বড়। কারণ, রাজনৈদিক দর্শন বিনোদন সংস্কৃতির রূপরেখাতেও পরিবর্তন আনতে সক্ষম। ধর্ম ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিধায় মসজিদ, মাদরাসা খানক্বাহ্, মাজার ইত্যাদিতে নিয়োজিত কর্মীরাও সংস্কৃতি কর্মী। এভাবে মানব সমাজে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আওতায় নিয়োজিত হয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত রয়েছে এ সমাজের অসংখ্য মানুষ এসব শাখা-প্রশাখার প্রায় সব মানুষও সংস্কৃতিকর্মী। হ্যাঁ, যেহেতু পরিশ্রুত উৎকর্ষিত জীবন চেতনাকেই সংস্কৃতির বিবেচনাতে ধরা হচ্ছে, সেহেতু এসব কর্মকান্ড অবশ্যই ওই মূল্যবোধের আওতায় হওয়া অপরিহার্য।
সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের ধর্ম-কর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, আইন-বিচার, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ধরণ, নাটক, সিনেমা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, কথার ধরণ, ব্যবহৃত জিনিষপত্র, লোক গাঁথা, ঐতিহ্য-প্রথা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র থেকে পরিবার পর্যন্ত আচরিত যাবতীয় বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের সাথে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে মিল-অমিল রক্ষা করে বহমান আছে, তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি, বাঙালি সংস্কৃতি। দেশগত এবং ধর্মীয় পার্থক্যের কারণেই আজ বাংলাদেশের বাঙালি সংস্কৃতির সাথে কোলকাতার বাঙালি সংস্কৃতির রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য।
ইসলামী সংস্কৃতি কী
উপরোক্ত মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায় যে, ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত মানবজাতির জীবনঘনিষ্ট যাবতীয় কর্মকান্ডই ইসলামী সংস্কৃতি। যেহেতু মূল্যবোধ সংস্কৃতির প্রাণ, তাই ইসলামী মূল্যবোধ পরিপন্থী জীবনাচারকে অপসংস্কৃতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। মদপান, ঘুষ খাওয়া, জুয়া খেলা, ব্যভিচার, অশ্লীলতা সবই অপসংস্কৃতি, যদিও তা মুসলিম সমাজে আচরিত হোক না কেন। অপরপক্ষে, অমুসলিম সমাজে প্রচলিত থাকলেও সত্যবাদিতা, শালীনতা, মেহমানদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, পরোপকারে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদিকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ঈমান না থাকার কারণে এসব ইসলাম সম্মত কাজ করার পরও তারা মুসলিম নয় বটে। তবুও তাদের আচরিত অভ্যাসকে ইসলামি সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। যেহেতু, ব্যক্তি থেকে সমাজে সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়, সুতরাং এর বিকাশ ঠিকানা হযরত আদম-হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং পরিপূর্ণতা এসেছে শেষ নবী সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাতে, সাহাবা, তাবে‘ঈন, আহলে বায়ত, সূফী, দরবেশ, আউলিয়া ও সচেতন আলেম-ওলামা এবং তাক্বওয়াবান মুসলমানদের হাতে। এর সৌন্দর্য ও পরিধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে চলছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকবে।
ব্যক্তি যখন ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেন, তখন তাঁর পরিশীলিত আচরণ-অভ্যাস ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে গৃহীত হতে থাকে। এভাবেই সংস্কৃতির এক একটি সোপান গড়ে উঠে। নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর অনুসরণে তাঁদের উম্মতের সমাজ ও উত্তম ইসলামি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার লাভ করেছে এভাবেই।
আবার, সমাজ থেকেও ব্যক্তিতে, সমাজ থেকে অপর সমাজেও সংস্কৃতি স্থানান্তরিত হতে পারে। যেমন, শিশু মুসলিম সমাজে জন্ম নেওয়ার সুবাদে সংশ্লিষ্ট সমাজ থেকে ইসলামি রীতিনীতি শিখে নেয়। দীর্ঘদিন মুসলিম সমাজে বসবাসের কারণে অমুসলিমরাও অনেক সময় মুসলিম সমাজের রীতিনীতিতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠতে পারে। বিশেষত অন্য সম্প্রদায়ের ভালো রীতি-নীতিকে গ্রহণে ইসলাম আপত্তি করেনা, যদি তা ক্বোরআন-সুন্নাহর পরিপন্থি না হয়। আর এ কারণেই ইসলাম জাহেলী যুগের অনেক পরিশ্রুত আচার-আচরণকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যখন যে দেশ আয়ত্ব করেছে তখন সে দেশের স্থানীয় সংস্কৃতির ভালো উপাদানগুলোকেও অনুমোদন দিয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। আর এই উদারতাই ইসলামকে দিয়েছে মহাবিজয়, ইসলামি সংস্কৃতির ভান্ডারকে করেছে মহাসাগরের মতো গভীর ও বিশাল।
ইসলামী সংস্কৃতির বিবর্তন ও রূপরেখা
ইসলামী সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের ব্যাপক পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে মূলত: ইসলামের চার দলীলের ভিত্তিতে- কিতাবুল্লাহ্, সুন্নাহ্, এজমা’ ও ক্বিয়াস। ক্বোরআনুল করীম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম মারফত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরিত আল্লাহর বাণী বা ‘ওহী’। ‘সুন্নাহ্’ বলতে বুঝাচ্ছি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম, বাণী ও অনুমোদন, যেগুলো খোদ্ রসূলের পাকের জন্য খাস নয়; উম্মতের আমল করার জন্য প্রযোজ্য।
এগুলো ছাড়াও খোলাফা-ই রাশেদীন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু, হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু এবং হযরত শেরে খোদা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সুন্নাতসমূহও ‘সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত। ক্বোরআন- সুন্নাহ্ মূলত আল্লাহরই পক্ষ হতে এসেছে। এ দু’টি ইসলামি সংস্কৃতির মৌলিক ভিত্তি। এ দুই ভিত্তি’র আলোকেই ইজতিহাদ বা গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যমত হলো এজমা’। ক্বোরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা’র অনুসরণে ক্বিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত পরিবেশ, সমস্যা ও পরিস্থিতির আলোকে গবেষণা করে ক্বিয়াস বা অনুমান ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠবে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি বির্নিমাণের অবারিত ধারা চলতে থাকবে, যা কখনো শেষ হবে না। উল্লেখ্য, বর্ণিত উৎসগুলো শেষ নবী হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে ধরা হয়। তাছাড়া, সংস্কৃতির ধারা, প্রথম নবী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম পুরুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং প্রথম নারী হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম’র জীবনাচার’র বিবর্তন’ ও আজকের সংস্কৃতির আদিতম উৎস, যা তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ কর্তৃক অনুসৃত হয়ে এবং তাদের মধ্যে সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হয়ে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই রূপরেখা অনুসরণ করেই সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ মানব সমাজের ¯্রােতে ভেসে কালের শেষ সীমানা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। যদিও এ সাংস্কৃতিক ধারা আদম-হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম’র মাধ্যমেই সর্বপ্রথম এ দুনিয়ায় প্রবেশ করে, পক্ষান্তরে একটি প্রশ্ন থেকে যায় ‘অপসংস্কৃতি’ সম্পর্কে। অপসংস্কৃতির উৎস ও বিকাশ কিভাবে হলো- এ প্রশ্নটিকে আমরা সূত্রবদ্ধ করে দেখাতে চাই। আর এর সহজ উত্তর হলো এই যে, এ অপসংস্কৃতির উৎস এর বিকাশ মানুষের আদি শত্রু ইবলীসের মাধ্যমে। আল্লাহর বিধান ও নির্দেশের প্রতি বিনা প্রশ্নে অনুগত হওয়ার ফেরেশতা সূলভ আচরণ এবং এর বিপরীতে আনুগত্য প্রত্যাখ্যানকারী অহংকারী শয়তানী আচরণ এ উভয় বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীতে বিকশিত হয় এ পৃথিবীতে। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণ তথা আল্লাহর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এ ফেরেশতা মনোভাবের বিকাশ ঘটতে থাকে, যাঁর নামই সংস্কৃতি বা ইসলামী সংস্কৃতি। আর পরবর্তীতে ইবলিস শয়তানের প্ররোচণায় ¯্রষ্টা বিস্মৃত পথভ্রষ্ট মানব সমাজের মাধ্যমে প্রসারিত বিশ্বাস ও আচার-আচরণই হলো অপসংস্কৃতি।
সুতরাং সংস্কৃতি নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে আসা এক মহান নি’মাত যা দুনিয়াকে জান্নাতের মরূদ্যানে পরিণত করতে পারে। আর পক্ষান্তরে, অপসংস্কৃতি হলো শয়তানী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ যা সৃষ্টির সেরা মানুষকে নিকৃষ্ট জীব-জানোয়ারের পর্যায়ে নামিয়ে দুনিয়াতে অশান্তি ও আখিরাতে কষ্টদায়ক ভয়াবহ্ নরক যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত করে। মানুষ নবীগণের শিক্ষায় সংস্কৃতিবান হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। আর শয়তানী প্ররোচনায় নিজের মনগড়া বিশ্বাস ও আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বিতারিত ইবলিসের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কারণে আল্লাহর গজব ডেকে আনে। উল্লেখ থাকে যে, সেদিন আদম আলায়হিস্ সালামকে সম্মান না করার অপরাধে বিতাড়িত ইবলিস, তার হাজার হাজার বছরের ইবাদতের বদলা হিসেবে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে এমন একটি ক্ষমতা অর্জন করেছিল, যেন সে মানুষের একটি বিশাল অংশকেও প্ররোচনা দিয়ে তার সঙ্গী হিসেবে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। তার এই শক্তির মহড়া সেদিন থেকে শুরু হয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে।
এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে একদল নবীগণের আদর্শে সংস্কৃতিবান হয়ে জান্নাতের দিকে আর অপরদল শয়তানের অপসংস্কৃতিতে মগ্ন হয়ে জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। আল্লাহর খলীফাগণ সত্যের দিকে আর শয়তান তার বিপরীতে নেতৃত্ব দিয়ে পৃথিবীর ধাবিত করবে। মানুষ যখন সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে, শয়তানের প্ররোচনায় নিজের ভালো-মন্দের বিধান নিজেরা তৈরী করে পৃথিবীতে অশান্তি-হানাহানি বাড়িয়ে দেয়, ঠিক তখনি আল্লাহ্ পাক তাঁর সে বান্দাদের ফিরিয়ে আনতে পাঠিয়ে দেন উক্ত অঞ্চলের মানুষের একই ভাষাভাষি কোন নবী রাসূল আলায়হিমুস্ সালামকে। এভাবে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত তিন লক্ষ ছয়ত্রিশ হাজার পর্যন্ত খলীফা প্রেরণের কথা আমরা জেনে আসছি। যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর আর কোনো নবী প্রেরণ করবেন না, সেহেতু তাঁর হাতেই দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করা হয়; যাতে করে মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামের সংস্কৃতি অতিক্রম করার কোনো প্রয়োজন না হয়।
প্রাক- ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি
প্রাক-ইসলামী যুগ বলতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন’র আগের সময়কে বুঝানো হয়। এ সময়কে আইয়্যামে জাহেলিয়াতও বলা হয়। এ সময়ের নবী ছিলেন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পাঁচশত বছর পরের এ সময় (৫১০-৬১০ খ্রিস্টাব্দ) সাধারণত: আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকারের যুগ’ হিসেবে পরিচিত। (P.k. Hitti, History of the Arabs)
হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর পর তাঁর উম্মতগণ খোদায়ী বিধান ছেড়ে ধীরে ধীরে আবারো শয়তানের তাঁবেদার বনে যায়। তারা আল্লাহর কিতাব পবিত্র ইঞ্জীলকেও নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধানুযায়ী পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলে। এভাবে পাঁচশ’ বছরের এ সময়ে ঈসায়ী ধর্মের আর কোনো অক্ষত-অবিকৃত নিদর্শনের অস্তিত্ব পাওয়া না যাওয়ায় ধর্মের নামে পৌত্তলিকতা এবং হিংসা ও হানাহানি এ ভয়াবহ রূপ লাভ করে। পরিশ্রুত মানবিক জীবন-যাপনের খোদায়ী বিধানের অবর্তমানে মানুষ নানা ধরনের অপসংস্কৃতি ও পাপাচারে অভ্যস্থ হয়ে পড়ে। জ্ঞান সাধনা, তথ্য অনুসন্ধান, সুস্থ বিনোদন, পরিবার ও সমাজব্যবস্থা সবকিছুই নির্বাসিত হয়েছিল দুনিয়া থেকে। সে যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি ইউরোপীয়দের কোন শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থপাঠ করাকেও সহ্য করা হতোনা। শিক্ষিত লোক এবং পাঠাগার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে J.W. Draper তাঁর intellectual Development in Europe গ্রন্থে বলেন, ‘‘খ্রীষ্ট ধর্মের যুগে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবীকে গোলাকার বলা ছিল অপরাধ। ঠিক সেই যুগের অজ্ঞতার কারণেই হিপাশিয়ার Hypatia দেহকে তাঁহার জ্ঞান পিপাসার জন্য আলোকজান্দ্রিয়ার গীর্জায় খন্ড-বিখন্ড করা হইয়াছিল। গ্যালিলিওকে রোমের গীর্জায় আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল। কোন লোকই নিজের সম্পদ, জীবন বা দেহের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া প্রচলিত মতবাদের উপর সন্দেহ পোষণ করিতে পারিতনা। ফলে কোথাও কোন আইন প্রণেতা, দার্শনিক ও কবির আবির্ভাব ঘটে নাই।’’ [কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ.-২০৭] বাইবেলের বিকৃতরূপ তুলে ধরে গীর্জা ভিত্তিক স্বার্থান্বেষী পুরোহিতরা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে সেদিন সংস্কৃতির বিকাশের সকল দরজা শক্তহাতে বন্ধ করে রেখেছিল। সেদিনকার ইউরোপের অন্ধকার যুগ সম্পর্কে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিল। অধ্যাপক কে. আলী তাঁর ‘মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস’ গ্রন্থে অপর এক ঐতিহাসিকের সূত্রে বলেন, ‘‘মহান গ্রেগরি রোম হইতে সকল শিক্ষিত লোককে বহিস্কৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে অগাষ্টাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দর্শন শাস্ত্রের পাঠাগারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার কুশাসনে গ্রীক ও রোমান গ্রন্থ পাঠ ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল।’’ লেক্ বলেন, সপ্তম শতাব্দিতে ইসলাম চিন্তার স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ইউরোপে জ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পূর্বে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুপ্তাবস্থায় ছিল। পুরোহিতদের মধ্যে শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নানা কুসংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।’’ [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮]
ঐতিহাসিকদের মতে, সে যুগে তুলনামূলকভাবে আরবের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য-জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ইউরোপের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল আরবরা। আরবদের উন্নত ভাষা সম্পর্কে পি.কে. হিট্টি HISTORY OF ARABS গ্রন্থে বলেন, ‘‘এই ভাষাই (আরবী) মধ্যযুগে বহু শতাব্দি ধরিয়া সভ্য বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতি চেতনার বাহন ছিল।’’ তিনি বলেন, ‘‘পৃথিবীতে সম্ভবত, অন্য কোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশী স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করে নাই এবং কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা এত আবেগাচ্ছন্ন হয়নাই।’’ হযরত জালালুদ্দিন সুয়ূত্বী তাঁর ‘আল-মুযহির’ ২য় খন্ডে বলেন, ‘‘কবিতা আরবদের সার্বজনীন পরিচয়ের স্বাক্ষরিত দলিল।’’
R.A. Nicholson তাঁর A Literary History of the Arbs গ্রন্থে আরবদের কবিতা প্রীতি সম্পর্কে বলেন, ‘সেই যুগে কবিতা কিছু সংখ্যক সংস্কৃতিমনা লোকের বিলাসিতার বস্তু ছিল না, বরং ইহা ছিল তাহাদের সাহিত্য প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম।’ [সূত্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯, ২১০] প্রাক-ইসলামী যুগের ‘উকাযের বার্ষিক মেলায় যে কবিতা উৎসব ও প্রতিযোগিতা চলতো তা আজ সকল কবিতাপ্রেমীদের জানা। সে যুগের এ বার্ষিক মেলায় সাতটি নির্বাচিত গীতি কবিতাকে সোনালী অক্ষরে লিখে কা’বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। এ সাতটি নির্বাচিত কবিতার নাম ‘সাব‘ই মু‘আল্লাক্বাহ্’। আধুনিক যুগেও প্রাচীন আরবের ওই সাব্‘ই-মু‘আল্লাক্বাহ্’ সেরা কবিতাগ্রন্থ এবং সে যুগের সেরা কবি ইম্রুল ক্বায়স আরবদের শেকেস্পিয়ার হিসেবে পরিচিত।
উল্লেখ্য, যখন ইউরোপে গীর্জার বাইরে জ্ঞানার্জনের রাস্তা বন্ধ রাখা হয়েছিল, সে সময়েও আরবের শ্রেষ্ঠ ও অভিজাত ক্বোরাঈশ বংশে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত আলী ইবনে আবী তালিব, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মতো শিক্ষিত পুরুষ এবং হযরত হাফসা ও উম্মে কুলসূম রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমার মতো শিক্ষিত নারী’র মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা ছিল। আর এ সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের পরবর্তী সময়ে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের বিধি-বিধান তথা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে লিপিবদ্ধ করণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন।
শিক্ষা-সংস্কৃতির কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের চেয়ে আরব’রা এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাজনৈতিকভাবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় গোত্র ভিত্তিক শাসনের এ যুগে গোত্রে-গোত্রে শত্রুতা ছিল বংশ পরম্পরায়। এক গোত্রের বিরুদ্ধে অপর গোত্রের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং এর পরিণামে সমগ্র আরব বিশেষত: নজদ ও হিজায ছিল রক্তারক্তি ও হানাহানির এক নিয়মিত ময়দান। বহুধা বিভক্ত এ আরব সমাজে আইনের শাসনের পরিবর্তে ‘জোর যার মুল্লুক তার’ বিধানই প্রচলিত ছিল সর্বত্র।
সামাজিকভাবে নানা প্রকারের কুসংস্কার সমগ্র আরবকে জাহেলিয়াতের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রেখেছিল। দেব-দেবীর সন্তুষ্টি পেতে বেদীমূলে নরবলি ছিল সে সমাজের স্বাভাবিক সংস্কৃতি। নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা সে যুগে আরব বা অন্য কোথাও কল্পনা করা যেত না। বহু পতœী ও বহুপতি প্রথা আরবের সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে পশুর মতো ব্যবহার করা হতো। সুদ, মদ, জুয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যাসহ অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত ছিল মানুষ। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে অপমানের চোখে দেখা হতো সামাজিকভাবে। তাই জন্মদাতা পিতা স্বহস্তে জীবিত কবর দিতো নিজের শিশু কন্যাকে। বিধবা বিয়ে ও সম্পত্তিতে নারীর অংশ কল্পনা করা যেত না। অধিকন্তু ধর্মীয় বিশ্বাসের আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে তারা বায়ু, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাথর, বৃক্ষ ও মূর্তির পূজাতে লিপ্ত ছিল। W.Muir তাঁর Life of Muhammad গ্রন্থে বলেন, ‘স্বরণাতীত কাল হইতে মক্কা ও সমগ্র আরব উপদ্বীপ আধ্যাত্মিক আসারতার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল-মূর্তি পূজাই ছিল তাহাদের ধর্ম’। [প্রাগুক্ত, পৃ. ৪]
কা’বা ঘরে ‘হুবল’সহ ছোট বড় ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করে তাদের পূজা করত এবং বলত যে, ‘‘আমরা কেবল ইহাদের পূজা এই জন্যই করিতেছি যে, ইহারা আমাদিগকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবে’। [আল-ক্বোরআন: ৩৯ঃ৩] এ সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনে অপর আয়াতে বলা হয় যে, ‘‘বেদুইন আরবদের মধ্যে কুফর ও মুনাফেক্বী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।’’ [আয়াত ৯ঃ৯৮] মোটকথা, ‘হাজরে আসওয়াদ’ (কালো পাথর) চুম্বন এবং খানায়ে কা’বার তাওয়াফের মতো কিছু মৌলিক সংস্কৃতির অনুসরণের পাশাপাশি তাদের মধ্যে ছিল অসংখ্য অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা। সে সময়ে হযরত আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু, হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুসহ কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য পাপাচার মুক্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করলেও অধিকাংশরা ছিলো শির্ক ও অন্যান্য গর্হিত কাজে অভ্যস্ত। ঠিক এমন সময়েই ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর মনোনীত সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে ইসলামের সূচনা।
ইসলামের বিস্ময়কর সূচনা
‘ইক্বরা’ বা ‘পড়’ শব্দ দিয়ে ইসলামের প্রথম ঐশী বাণী পৃথিবীতে বিদ্যমান তৎকালীন সময়ের সকল অজ্ঞানতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। শিক্ষার লক্ষ্য যাতে লক্ষ্যহীন হয়ে নিছক ভোগ-বিলাসের উপায়ে পরিণত না হয় সে জন্য প্রথম আয়াতেই এর নীতি নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, ‘ইক্বরা’ বিস্মিরাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব’- পড়! তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।’’ [সূরা আলাক্ব] এ আয়াতেই আমাদের শিক্ষানীতি যে ধর্ম নিরপেক্ষ হতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম শুধু ‘ইক্বরা’ শব্দ বারবার বলার পরও তা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখে উচ্চারণ করেননি। সম্পূর্ণ আয়াত অর্থাৎ ‘পড়–ন আপনার রবের নামে’ বলার পরই তিনি পড়তে শুরু করলেন। এ ঘটনা থেকেও ধারণা করা যায় যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি হবে ¯্রষ্টা নির্দেশিত কাঠামোকে অনুসরণ করে। এর পরের আয়াতেই বলা হয়েছে, ‘খালাক্বাল ইনসানা মিন আলাক্ব’ অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ‘আলাক্ব’ তথা অপবিত্র তরল পদার্থ বা শক্রু থেকে; যা একদিকে মানুষকে তার সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে অন্যদিকে মানুষকে বানরের জাত বানানোর মতো অপমানকর ডারউইনের বিবর্তনবাদ (Theory of Evelution) কে বাতিল করে দিয়েছে। সৃষ্টির সেরা মানব যাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ফেরেশতা ও জিন জাতির উপর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত; তাদেরকে ইতর প্রাণী বানরের সংস্করণ হিসেবে প্রদর্শন করা আর সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিভ্রান্তিতে ফেলা একই কথা। পৃথিবীতে অসংখ্য সৃষ্ট জীব-জানোয়ার রয়েছে, রয়েছে কীট-পতঙ্গ। এদেরও নিজস্ব জীবনধারা, আচার-আচরণ ইত্যাদি রয়েছে। তাদের এ জীবনাচারকে সংস্কৃতি বলা হয়না। সংস্কৃতি বলা হয় শুধু মানুষের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবন যাপন প্রণালীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ডকে। ‘বানরের জাত’ প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে অধঃপতিত করে বানর-শিয়াল-শুকরের আচরণে উৎসাহিত করবে। কারণ সংস্কৃতির নামে শিকড় সন্ধানের যে শ্লোগান বর্তমানে ওঠেছে সে সূত্র ধরে পিছনে যেতে যেতে বানরের বাঁদররামিটাই শুধু পাওয়া যাবে। ঐতিহ্য প্রিয় এ বানরের জাত কীভাবে একটি সুশৃঙ্খল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে? কখনো সম্ভব নয়। তাইতো এ দুনিয়ায় ‘আশরাফুল মাখলূক্বাত’ মানুষগণ সৃষ্টি করে চলেছেন ‘সংস্কৃতি’; আর বানরের জাতরা জন্ম দিচ্ছে সংস্কৃতি ও বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতি বিকাশের অসংখ্য সন্তান। এ সন্তানদের হাতেই আজ বাংলাদেশটা পরিণত হচ্ছে সন্ত্রাস-ধর্ষণ-অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার এক আঁধার জগৎ এবং বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও লক্ষ্যহীন হিং¯্র জন্তু-জানোয়ারের এক অভয়ারণ্য।
আশরাফুল মাখলূক্বাতের এ চরম অবনতি ঠেকাতেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ আল-ক্বোরআন মানব জাতিকে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে সত্য, ঐতিহ্য ও উন্নয়নের পথ বের করার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। সূরা আলাক্বের অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে সে পড়ালেখার কথা এবং মানবজাতির মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের কথা। বলা হয়েছে, ‘‘পড়–ন ওই প্রভুর নামে, যিনি মানুষকে সম্মানিত করেছেন, কলমের ব্যবহার শিখিয়েছেন এবং যা সে জানতোনা সবকিছু শিখিয়েছেন ইত্যাদি। যা ইসলামী সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতিকে একটি সুন্দর রূপরেখার মাধ্যমে পরিচালনার পথ নির্দেশ করেছে। আল-ক্বোরআন সর্বশেষ ঐশী কিতাব। এরপর আর কোনো মৌলিক ধর্মগ্রন্থ আসবেনা বিধায় একে পরিপূর্ণতা দেওয়া হয়েছে। এতে সংযোজিত হয়েছে হযরত আদম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সময়ের উত্তম সংস্কৃতি এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির জন্য সম্ভাব্য কত উপাদান দরকার তার বর্ণনা। পূর্ববর্তী নবীগণ আলায়হিস্ সালাম ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং শেষ গ্রন্থ আল ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও সমাপনী বিষয়ে নিজ নিজ উম্মতকে অবহিত করেছেন। আর ক্বোরআনেও বর্ণিত হয়েছে পূর্ববর্তী নবীগণের জীবন ও কর্ম। মোটকথা, এটা আল্লাহর অপরাপর কিতাবগুলোর বিবর্তিত সর্বশেষ রূপ’ যা সকল কালের মানুষের পথ নির্দেশনার জন্য নির্ধারিত। ক্বোরআন আরবী ‘ক্বারউন’ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হচ্ছে একত্রে সন্নিবেশিত করা। এর অন্য অর্থ হলো পাঠ করা বা আবৃত্তি করা। এতে সকল ধর্মের অবিকৃত উত্তম সংস্কৃতির সংযোজন হয়েছে এবং এ গ্রন্থ পাঠ করলে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও সংস্কৃতি আয়ত্ব করা সম্ভব হবে, তাই এর নামকরণ হলো আল-ক্বোরআন। ক্বোরআনের ভাষায় এর অন্যান্য নামও পাওয়া যায়। যেমন, আল-কিতাব অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ, আল ফোরক্বান অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যকারী। এতে আল-হিকমত (বিজ্ঞান), আল-হুকুম (বিচার), আর-রহমত (কল্যাণ), আন্ নি’মাত (আর্শীবাদ), আন নূর (আলো), আল-হক্ব (সত্য) ইত্যাদি বলা হয়েছে, যা আল ক্বোরআনের পূর্ণতা নির্দেশক। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর বাণী ছিল, ‘এখনও আমার অনেক কথাই বলিবার রহিয়াছে, কিন্তু তোমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। যাহা হইক, যখন তিনি সত্যের চেতনা শক্তি আসিতেছেন, তখন তিনিই তোমাদিগকে সকল সত্যের পথে পরিচালিত করিবেন’ যা শেষ নবীর আগমন, পূর্ণতা ও সত্যের বিবর্বিত রূপ’র একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।
ইসলামে পূর্ববর্তী সময়ের সংস্কৃতিকে যে লালন করা হয়েছে তার উজ্জ্বল প্রমাণ ক্বোরআনে রয়েছে। বলা হয়েছে, ‘তোমরা বল! আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যাহা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক্ব ও হযরত ইয়াক্বুব আলায়হিমুস্ সালাম এবং তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে যাহা প্রদান করা হইয়াছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাঁহাদের প্রতিপালক হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তদসমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি; তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আমরা প্রভেদ করিনা এবং তাঁহারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।’’[আল ক্বোরআন: ২: ১৩৬]
উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম আল্লাহর বিধানসমূহের সর্বশেষ সংস্কারণ। এতে হযরত আদম-হযরত আলায়হিমাস্ সালাম থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সময়ের বিবর্তনের সৃষ্ট সকল উত্তম সৃষ্টি সভ্যতাকে ধারণ করা হয়েছে। আর এ সময়ে শয়তানী মেধার কুফলে সৃষ্ট সকল অপসংস্কৃতিকেই শুধু বাদ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সকল ধর্মের সত্যকে লালন করে, ভ্রান্তি সংশোধন করে, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকে সুস্পষ্ট করে পৃথিবীর সর্বশেস সময় পর্যন্ত কালের চাহিদা মেটানোর উপযোগী কল্যাণকর যে গ্রন্থ লালন করেছে তাই আল ক্বোরআন। আল ক্বোরআন’র এই চিরন্তন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি অমুসলিম দার্শনিকরাও দিয়ে আসছেন। টলস্টয় বলেন, ‘ক্বোরআন মানবজাতির শ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক দর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থ থাকতো এবং কোন সংস্কারকই না আসতেন, তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটাই ছিল যথেষ্ট।’ [সূত্র. দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম ১৫/০১/২০০১ খ্রিষ্টাব্দ]
William Muir তাঁর Life of Muhammad গ্রন্থে’র ভূমিকায় বলেন, ক্বোরআনের ন্যায় পৃথিবীতে সম্ভবত, আর এমন একটি গ্রন্থও নাই, দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরে যার ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হয়ে আছে’। পৃথিবীতে ক্বোরআনের সমকক্ষ কোন গ্রন্তের অস্তিত্ব নেই, যাকে বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব। যাঁর অবিকৃতি সম্পর্কেও বিজ্ঞানের সূত্র প্রয়োগ সম্ভব। সম্প্রতি আবিস্কৃত ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’-এর ১৯ হরফ সংখ্যা দিয়ে কম্পিউটার পদ্ধতিতে ক্বোরআন-বিশ্লেষণের সূত্র অনুসন্ধানী অমুসলিম গবেষকদেরও আলোর পথ দেখাতে পারে।
মানব সমস্যার স্থায়ী সমাধান ছাড়া ও এর সাহিত্য মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত। এফ. আরবুথনট বলেন, ‘‘সাহিত্য শৈলীর বিচারে ক্বোরআন হইতেছে আধা-পদ্য ও আধা-গদ্যের সংমিশ্রণে বিশুদ্ধতম আরবীর নমুনা।’’ ‘দ্য- লা ভিনিসেটের উক্তি অনুযায়ী ক্বোরআন হইতেছে মুসলিম ধর্ম বিশ্বাসের সনদ ও গঠনতন্ত্র যাহা বর্তমান দুনিয়ার কল্যাণের প্রতিশ্রুতি এবং আখেরাতের মুক্তির আশ্বাস দিয়াছে। ক্বোরআনের সাহিত্যিক মূল্যমান সম্পর্কে ড. মরিস নামে আর একজন ফরাসী পন্ডিত বলেন, ‘ক্বোরআন বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বিজ্ঞান সংস্থা, ভাষাবিদদের জন্য একটি শব্দ কোষ, বৈয়াকরণের জন্য ব্যাপকরণ গ্রন্থ, কবিদের জন্য একটি কাব্যগ্রন্থ এবং আইন বিধানের এক বিশ্বকোষ। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থ ইহার একটি মাত্র সূরা’র সমকক্ষ বলিয়া ও বিবেচিত হয় নাই।’ [কে. আলী, মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃ. ২৭-২৮]
সুতরাং ক্বোরআনের সাহিত্য মূল্য বিবেচনা করলেও এর সাংস্কৃতিক মর্যাদা অনুধাবন করা যায়। সংস্কৃতি মানুষের বিশ্বাস ও কর্মকান্ডের সামগ্রিক একটি দিক। সুতরাং ইসলামের যাবতীয় বিশ্বাস ও বিধি-বিধানগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। পবিত্র ক্বোরআন হলো ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক তাত্ত্বিক গ্রন্থ এবং সুন্নাহ্ হচ্ছে এর বিশদ ব্যাখ্যা এবং ব্যবহারিক (Practical) ক্বোরআনের বক্তব্যগুলো ১১৪টি সূরায় বিন্যস্থ করা হয়েছে। এর ৯২টি মক্কী এবং ২২টি মাদানী সূরা। হিজরতের পূর্বে মক্কা জীবনে নাযিলকৃত সূরাগুলোতে আল্লাহর একত্ববাদ, ‘আল্লাহর গুণাবলী, মানুষের নৈতিক কর্তব্য, পরকালের শান্তিমূলক ইত্যাদি বিষয় এবং মাদানী সূরাতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রবিধান, বিধি-নিষেধ, আইন-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। মক্কী জীবনে এ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সত্ত্বা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রকৃত বিশ্বাস ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক ও আহ্বান করেছেন, আর মাদানী জীবনে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর মদীনা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সংস্কৃতি পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মক্কী জীবনে ধীরে ধীরে যে ক্ষুদ্র ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠেছিল তা হিজরতের পর মদীনায় এসে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপ নেয়। এখানে ইসলাম এক উদার বিশাল ¯্রােত ধারণ করে। পৌত্তলিক, ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নি উপাসকরাও এ রাষ্ট্রের মদীনা সনদে স্বাক্ষর করে ইসলামের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সমর্থন দিয়েছিলো। এ মদীনা সনদ’ই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। মদীনা রাষ্ট্রই পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্র যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত গোত্রগুলো সাথে নিয়ে একটি শাসনের অধীনে আনা হয়। এ রাষ্ট্রে যার যার ধর্ম-সংস্কৃতি ও গোত্র-সংস্কৃতিকে সম্মান করা হয়েছে। ভিন্নমতাবলম্বীদের জান-মাল ইজ্জত ও ধর্ম-সংস্কৃতির সার্বিক নিরাপত্তা প্রদানের কারণেই ইসলাম একটি উদার আদর্শ হিসেবে পৃথিবীতে সুনাম কুঁড়াতে পেরেছে।
ইসলামি সমাজ ও ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে সাংস্কৃতিক নীতির পার্থক্য দেখিয়ে কবি গোলাম মুস্তফা তাঁর ‘বিশ্বনবী’তে খুব সুন্দরই বলেছেন যে, ‘ইসলামি সমাজে দূর্গাপূজা চলা অসম্ভব আর ইসলামি রাষ্ট্রে দূর্গা পূজা বন্ধ করা অসম্ভব’। আসলেও তাই ইসলামি সমাজ মুসলমানদের একান্ত নিজস্ব পরিমন্ডল। আর ইসলামি রাষ্ট্র কাফের, বেদ্বীন মুসলমান, নাস্তিক সবার জন্য। এতে সবার সাংকৃতিক অধিকার সমান।
হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এক দশকের রাষ্ট্রীয় জীবনে মানব সভ্যতার সর্বশেষ প্রয়োজনের দিকটিও বিবেচনা করে আল্লাহর বিধান আল ক্বোরআন এসেছে এবং রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে তিনি নিজের এ ক্বোরআনের ব্যাখ্যা ও নিজের সাংস্কৃতিক জীবনের যে আদর্শ রেখে গেছেন তাই সুন্নাহ্ হিসেবে পরিচিত। ক্বোরআন সুন্নাহ’র আলোকে পরবর্তী সময়ে ইসলামকে গবেষণার অবারিত সুযোগের মাধ্যমে একে কালজয়ী করা হয়েছে। বিদায় হজ্জের সময়ে তাই এই দ্বীন-ইসলামের পূর্ণতার গ্যারান্টি সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়, ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (পরিপূর্ণ জীবন বিধান) হিসেবে মনোনীত করিলাম’। [আল ক্বোরআন- ৬:৩]
সংস্কৃতি হল মানব সমাজের সামগ্রিক আচার-আচরণ। সুতরাং ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত সেই পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃতি বা দ্বীন যা পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক আরো সুবিন্যস্থ হয়ে এবং বিভিন্ন মাযহাবের মাধ্যমে বৈচিত্র্য অর্জন করে এং বিভিন্ন সূফী ত্বরিকা এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিত্য নতুন সৌন্দর্য লাভ করে প্রচারিত ও প্রসারিত হচ্ছে।
ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা
ক্বোরআন, সুন্নাহ, এজমা’ ও ক্বিয়াস’ই ইসলামি সংস্কৃতির উৎস। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো- ঈমান, নামাজ, রোযা, হজ্ব ও যাকাত। এগুলোকে আমরা ইসলামের মৌলিক এবং বাধ্যতামূলক সাংস্কৃতিক উপাদান বলতে পারি। সঠিক বিশ্বাস বা আক্বিদার উপরই ঈমানের বাস্তবতা নির্ভর করে। ঈমান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, কিতাবসমূহ (পূর্ববর্তী এবং বর্তমান), নবীগণ (পূর্ববর্তীসহ) পরকাল সম্পর্কে, তাক্বদীর তথা অদৃষ্টের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরূত্থান সম্পর্কে সঠিক আক্বিদা (যথাযথ বিশ্বাস) প্রতিষ্ঠা। উপরোক্ত সপ্ত বিষয়ের যে কোনটিতে ব্যতিক্রম আক্বীদা পোষণকারী’র ঈমানের অস্তিত্ব প্রশ্নে সংশয় সৃষ্টি হয়। নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত শুধুমাত্র ঈমানদারের জন্যই নির্ধারিত। নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি পূর্ববতী নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর সময়েও পালিত হতো, তবে বর্তমানের মতো এতো সমৃদ্ধ ও সুসংহত ছিল না। নামায মুসলমানদের প্রধান সংস্কৃতি। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের একজন নামাজিকে দেখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক বুঝে নিতে পারে যে উনি মুসলিম। দৈনিক পাঁচওয়াক্ত শুক্রবারে জুমা এবং ঈদ-জানাযা ইত্যাদি নামাযের মাধ্যমে বিশষত জামাতসহ আদায়ের রীতি মুসলমানদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে সুসংহত করেছে। মুসলমানদের এ সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতে মুক্তি হলেও তা শারীরিক সুস্থতার জন্য হালকা যোগ ব্যায়ামের কাজও করে। এখানেই ইসলামী সংস্কৃতির সার্থকতা। রোযা পালনের মাধ্যমেও শারীরিক সুস্থতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান খালিপেটে থাকার একটি নিয়মিত ব্যবস্থাকে শারীরিক সুস্থতার জন্য অপরিহার্য মনে করছে। তাছাড়া ‘কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায়, জীবনে যাদের হররোজ রোজা-ক্ষুধায় আসেনা নীদ’ এমন অভাবী-অনাহারী প্রতিবেশির ব্যথা অনুধাবনের একটা ব্যবস্থাও এই রোযা। আবার ইফতার পার্টি তো আজকাল সার্বজনীন উৎসবে পরিনত হচ্ছে। সুতরাং রোযা সাংস্কৃতি আমাদের সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। হজ্ব’ বিশ্ব ইসলামী সংস্কৃতির একটি রূপ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ উপলক্ষে মক্কায়ে মুয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় সমবেত হয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে কতিপয় নির্ধারিত কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই একই আওয়াজে গেয়ে যাচ্ছে ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শরিকা লাকা লাব্বাইক… খানায়ে কা’বা তাওয়াফ করছে, চুমু খাচ্ছে হাযরে আসওয়াদে। সাফা-মারওয়া সা‘ঈ (দৌঁড়াদৌঁড়ি) করছে। ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের ময়দানে বক্তব্য শুনে নামায পড়ছে দুই ওয়াক্তকে একত্র করে। রাত যাপন করছে মুয্দালিফা নামক পাহাড়ে এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায় করছে। আবার লক্ষ লক্ষ হাজী ফিরে আসছে মিনার তাঁবুতে। সেখানে শয়তানের কল্পিত প্রতিকৃতিতে তিনদিন পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ে মারছে। কোরবানী দিচ্ছে। মাথা মুন্ডাচ্ছে। কি এক অপরূপ দৃশ্য। এ সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বের নানা রঙের নানা জাতের নানা মাযহাবের মুসলমানদেরকে এক কাতারে শামিল করে বিশ্বের সকল ঈমানদার ভাই-ভাই এ মূল্যবোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে। যাকাত ইসলামি অর্থনীতি উন্নয়নের এক গতিশীল ব্যবস্থা। ধনীদের পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত ধন-সম্পদ, টাকা পয়সা প্রতি বছরে একবার অভাবী ও বঞ্চিতদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়ার এ সংস্কৃতি পৃথিবীর অন্য কোন বিধানে বিরল। ধনী-গরীবের ব্যবধান কমিয়ে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার এ অঙ্গীকার শুধু ইসলামী সংস্কৃতিতেই রয়েছে। এখানে সংস্কৃতি পালনের উদ্দেশ্য একই সাথে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। এখানেই অন্যান্যদের সাথে ইসলামের পার্থক্য।
উপরোক্ত ফরয সংস্কৃতির বাইরে রয়েছে অসংখ্য ওয়াজিব সুন্নাত, নফল মুবাহ ধরনের সংস্কৃতি। যা একজন সাধারণ ঈমানদারকে পরিপূর্ণ মুসলিম হয়ে কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা। [সূরা আল-ই ইমরান] পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে কবরে যাওয়ার জন্য মুসলমানরা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল, মুবাহ্ সব ধরনের কর্মপালন করে আসছে। একজন মুসলিম কী করবে আর কী করবেনা তা নির্ধারণের জন্য হালাল এবং হারাম এ দু’ধরনের কর্মকান্ড নির্ধারিত আছে। যা করা ক্বোরআন-সুন্নাহ্ অনুসারে নিষিদ্ধ তাই হারাম। যা হারমা নয় তাই হালাল। এগুলোই প্রকৃত অর্থে গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি হিসেবে পালিত হবে। এ ছাড়া মুবাহ্ এবং মাকরূহও রয়েছে, যা করাতে গুনাহ্ নেই বরং নিয়ত গুণে সাওয়াব আছে তা মুবাহ, যা না করা উত্তম তবে গুনাহ্ নয় তা মাকরূহ। অবশ্য মাকরূহ ধরনের কাজগুলো তাহরীমী ও তানযীহী এ দু’ভাগে বিভক্ত। তাহরীমিকে চরম অপছন্দনীয় (গুনাহ্) এবং তানযীহীকে অপছন্দনীয় গণ্য করা হয়। সুতরাং ইসলামি সংস্কৃতির পরিধি বৃদ্ধিতে কোন কাজটি অপছন্দনীয় ও অপছন্দনীয়, কোনটি ইবাদত আবার কোনটি নিষিদ্ধ, কোনটা না করা উত্তম বিবেচনা করতে হবে। ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা অনুধাবনে আরো কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়কে বিবেচনা করতে হবে। একজন মুসলমানের যাবতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি তাওহীদ রেসালত ও আখিরাত’র প্রতি দৃঢ় আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর একত্ববাদ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনাদর্শ ধারণ করেই আখেরাতে মুক্তি সম্ভব। এ মূল্যবোধ ধারণ করেই ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো নির্মিত হয়ে আসছে।
হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরো প্রসারিত হয়েছে। এরপর থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে সমসাময়িক পরিস্থিতি ও সমস্যার আলোকে সমাধান দিতে এবং ইসলামের এ ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করতে জন্ম হয় হানাফী, শাফে‘ঈ, মালেকী ও হাম্বলী- এ চারটি মাযহাব। ঈমান আক্বীদার ক্ষেত্রে এ চার মাযহাবের কোন পার্থক্য নেই। শুধুমাত্র ফরয-ওয়াজিব-সুন্নাত-নফল সংস্কৃতিগুলো পালনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সামান্য পার্থক্য এদের মধ্যে রয়েছে। এ পার্থক্য মূল কাঠামোতে নয় বরং অতি কাঠামো বা উপরি কাঠামোতে (Super structure) হওয়ায় মুসলমানদের নির্ধারিত মৌলিক সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র এসেছে। যে যার পছন্দ অনুসারে একই সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাস স্থাপনের পর ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব অনুসরণ করতে পারে।
নিজ নিজ মাযহাব অনুসারে নি¤œস্বরে অথবা উচ্চস্বরে বলছে মাযহাবের পার্থক্য ইসলামের জন্য কল্যাণকর। এরা পরস্পর ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্তও নয়। কিন্তু আক্বিদাগত বিভ্রান্তির কারণে যে সব উপদল ইসলামের নামে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো ইসলামের মূলধারার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে। শান্তি ভঙ্গ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক রাস্তা মাত্র একটিই এবং একটি দলই জান্নাতে যাবে, বাকিরা বিভ্রান্ত হিসেবে দোযখী হবে। এ সংক্রান্ত একটি বহুল প্রচারিত হাদিস হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ‘বনী ইসরাইল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। বাহাত্তর দলই জাহান্নামে যাবে, একদল যাবে জান্নাতে। সাহাবা-এ কেরাম আরয করলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম কোন্ দলটি জান্নাতে যাবে? এরশাদ হলো, ‘মা’- আনা আলাইহি ওয়া আসহাবী, ‘আমি এবং আমার সাহাবীদের দল।’ [তিরমিযী]
উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর মিরক্বাত শরহে মিশকাত এ নাজাত প্রাপ্ত দলটিকে ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত’ বা সুন্নি মুসলমানদের দল হিসেবে চিহ্ণিত করেছেন। হযরত বড়পীর গাউসুল আ’যম আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু তাঁর ‘গুনিয়াতুত্ তালেবীন’-এ উক্ত নাজাতপ্রাপ্ত দলকে ‘সুন্নী জামা‘আত’ বলে উল্লেখ করেন এবং বাকি ৭২টি বাতিল ইসলামের তালিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এ বাতিল দলে রাফেজী, খারেজী, শিয়া, মু’তাযিলা, ক্বদরিয়া, জবরিয়া এভাবে ৭২টি দলের নামে রয়েছে। শিয়ারা অধিকাংশ সাহাবীকেই গালাগালি করার ধৃষ্টতা দেখায়। সুতরাং তারা সাহাবীদের অনুসারী হবার প্রশ্নই উঠেনা। পরবর্তীতে এ দলগুলো আরো বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে ইসলামের সাংস্কৃতিক ঐক্য নষ্ট করেছে। এ সমস্ত বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে ইসলামের মূলধারা সুন্নিয়তের অনুসারীদের রয়েছে সাংস্কৃতিক সংঘাত। বর্তমানে আছে শিয়া সম্প্রদায়, খারেজীদের নব্য সংস্করণ ওহাবী সম্প্রদায়, কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং মু’তাযিলাদের নব্য সংস্করণ মওদুদী সম্প্রদায়। ইসলামি আইনে শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক আইনসহ অনেক ক্ষেত্রে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, শিয়া’রা সাময়িক বিয়ে অর্থাৎ নেকাহ-ই মাত্‘আহ্ (Contact Marriage) কে নিজেদের সংস্কৃতির অংশ করে নিয়েছে, অথচ এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেই। কারণ, এটা নারী জাতিকে ভোগের পণ্যে পরিণত করে। শিয়ারা একদিকে ইসলামের দাবীদার অন্যদিকে খ্রিস্টান ইহুদীদের সাময়িক বিয়েকে লালন করে যাচ্ছে। সুন্নিরা ১০ মহররম পবিত্র আশুরা উপলক্ষে ফাতেহা-মাহফিল করে, তবাররুকের আয়োজন করে, শোহাদায়ে কারবালা’র তাৎপর্য শীর্ষক ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা করে, ওরস শরীফ উদ্যাপন করো আহলে বায়তের মর্যাদা তুলে ধরে। আর শিয়ারা কারবালার অনুসরণের নামে বুকে ছুরি চালানোর মতো অতি গর্হিত মাতম সংস্কৃতি পালন করে, যা সুন্নিরা নিন্দনীয় মনে করে। আশুরার মেলার নামে এরা কল্পিত এজিদ ও ইমাম হোসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মূর্তি তৈরি করে। শিয়ারা ইফতার করে এশা’ নামাযের সময়ে- অথচ সুন্নিরা করে সূর্যাস্তের পরপর। এরা ক্বোরআনের অনেক সূরাকে অস্বীকার করে আর অধিকাংশ হাদিসকেই বানোয়াট মনে করে। এ বিস্তর সাংস্কৃতিক পার্থক্য শিয়াদেরকে আলাদা একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেছে এবং বিশ্বব্যাপী সুন্নিদের সাথে তাদের সংঘাতকে অনিবার্য করে রেখেছে। সমাজ পৃথক হলে সংস্কৃতিও পৃথক হতে পারে। শিয়াদের সমাজও পৃথক হয়ে আছে।
শুধু শিয়ারা কেন, ক্বাদিয়ানীরাও আলাদা সমাজে বসবাস করে। তাদের মসজিদেও প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। তারা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীকেও নবী মানে বিধায় সুন্নিদের সাথে সংঘাত চলছে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী-এরপর অন্য কোনো নবী আসতে পারে না, এরপর ওলী, পীর, মুর্শিদ, মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) এবং ইমামগণই নবীগণের উত্তরসূরী হয়ে দায়িত্ব পালন করবেন অথচ এরা এ মৌলিক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করায় আলাদা ধর্ম-সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এদের সমাজ ও বিশ্বাসের পার্থক্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, ভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। ওহাবী সম্প্রদায় খারেজীদের উত্তরসূরী কট্টর-উগ্রপন্থী একটি নব্য উপদল। সউদী আরব (নজদ)’র ক্ষমতা দখল করে প্রায় ৭০ বছর যাবত এরা সুন্নি পরিচয়ে সুন্নিদের সাথে আক্বিদাগত সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী ও মুহাম্মদ ইবনে সউদকে হাতে নিয়ে, আর্থিক ও সশস্ত্র সহযোগিতা দিয়ে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের আড়ালে তুর্কী ভিত্তিক সুন্নি খেলাফতের অবসান ঘটানোর কৌশল হিসেবে ব্রিটিশ সা¤্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘ এক শতাব্দির প্রচেষ্টায় নজদ ভিত্তিক ‘ওহাবী আন্দোলনকারী’দের ক্ষমতায় বসায়। ওহাবীদের নজদ ভিত্তিক উত্থান নবীজি হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ভবিষ্যৎবাণী ‘নজদ থেকে শয়তানের শিং বের হবে’ (আল হাদিস) -এর যথার্থ বাস্তবায়ন। তাদের উত্থান মুসলমানদের বর্তমান ভয়াবহ পরিণতির প্রধান কারণ। তাদের কারণে তুর্কি খেলাফত ধ্বংস হলো এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর কোন নির্যাতিত দেশের পক্ষে এ সউদী আরব দাঁড়াতে পারেনি। কারণ, মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়াতে গেলে ব্রিটিশ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যেতে হবে। যারা ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে গেলে ফাঁস হয়ে যাবে অনেক তথ্য, অধিকন্তু হারাতে হবে ক্ষমতা। তাই, তারা বরাবরই খ্রিস্টান ইহুদীদের স্বার্থ রক্ষা করে ‘শয়তানের শিং’ হবার সত্যতা প্রমাণ করেছে। যে জজিরাতুল আরব থেকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বাইরে রাখার নির্দেশ রয়েছে, সেখানেই আজ ইহুদী-খ্রিস্টান তথা আমেরিকান পুরুষ-মহিলা সৈনিকদের মেহমানদারী করা হচ্ছে। এরা ক্ষমতায় এসেই সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছিল ভয়াবহভাবে। মুছে দিতে চেয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে।
পৃথিবীর দেশে দেশে যখন সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংরক্ষণের লক্ষে পুরোনো স্থাপনা, স্থাপত্য, নাম ফলক তথা বিভিন্ন নিদর্শন আবিস্কার, সংরক্ষণ করছে। পুরোনো নিদর্শন সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জাদুঘর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেখানে ওহাবীরা ক্ষমতায় এসেই প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরাম ও আহলে বায়তের স্মৃতি বিজড়িত তেরশ’ বছর আগের নজদ-হেযাযকে ইবনে সউদ এর নামানুসারে পরিবর্তন করে ‘সউদী আরব’ নামকরণ করলো। ‘নজদ থেকে শয়তানের শিং বের হবে’ এ ভবিষ্যৎ বাণী যাতে আর জীবিত না থাকে এ জন্য ‘নজদ’ স্থানটিকে ‘রিয়াদ’ বানানো হলো। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র রওযা মুবারকটি ধ্বংস করতে না পারলেও ওখানকার তেরশ’ বছরের স্মৃতিবাহী সকল মাযার-খানক্বাহ্ এমনকি মসজিদ পর্যন্ত মাটির সাথে মিশিয়ে নজীরবিহীন সাংস্কৃতিক সন্ত্রাস চালানো হলো। ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ওরস-ফাতেহাসহ সূফী দর্শন ভিত্তিক সংস্কৃতি কঠোর হস্তে দমন করা হলো এবং এসব সংস্কৃতির সমর্থকদেরও উচ্ছেদ করা হলো-মাতৃভূমি থেকে। আগের আরব আর সউদী আরব সাংস্কৃতিকভাবে বহুযোজন দূরে অবস্থান করছে মক্কা শরীফ দারুল ইলম কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। মদীনা শরীফের নতুন ও পুরাতন নিদর্শনাবলীর ইতিহাস সংক্রান্ত ৩৩৯ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি বইয়ে ৭০-৮০ বছর আগের বিভিন্ন মসজিদ, মাযার-গুম্বুজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ছবিসহ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরের ছবিসহ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে ওহাবী শাসকদের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসের ইতিহাস।
আল্লামা সৈয়্যদ আহমদ ইয়াসিন আল খাইয়্যারী আল মাদানী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি কর্তৃক লিখিত ‘তারীখু মা‘আলিমিল মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্ নামক এ প্রামাণ্য গ্রন্থটির ১৯৯১ সালে মক্কা শরীফ থেকে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ চট্টগ্রামের মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফি’র ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে আমি (লেখক) নিজেও দেখেছি। এছাড়াও দৈনিক আজাদী চট্টগ্রাম’র চীফ রিপোর্টার মুহাম্মদ ওবায়দুল হক গত ১৪ মার্চ ২০০২ তারিখে চট্টগ্রামের মুফতি ওবাইদুল হক নঈমী ও আমাকে (লেখক) একটি করে সেদিন মাত্র প্রকাশিত হওয়া একটি বই ‘সফরনামা’: আরব ও হেজায’-এর কপি সরবরাহ্ করেন। এ বইটি তাঁর দাদা হাটহাজারী থানার ধলই (হাধুরখিল) নিবাসী মাওলানা এয়ার মুহাম্মদ সাহেবের নিজ হাতে আজ থেকে ৮৮ বছর আগে লিখিত তাঁর নিজের আরব-হেজাজ সফরের বর্ণনা হিসেবে একটি ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল বটে। ১৫ জুন ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ (১৩২০) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভারত, মিসর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আরব ও হেজাজের বিভিন্ন নিদর্শন যেয়ারতে যাওয়ার ধারাবাহিক বর্ণনার সময়, দূরত্ব, যানবাহনের প্রকৃতি ও ভাড়াসহ পুঙ্খানুপুঙ্কভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন এতে এমন একটি সুস্পষ্ট নির্ভরযোগ্য দলিল দেখা যাচ্ছে, আজ থেকে মাত্র ৭০-৮০ বছর আগেও সেখানে অসংখ্য গুম্বুজওয়ালা মাযার ছিল। মাওলানা এয়ার মুহাম্মদ সাহেব ওহুদ প্রান্তরে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁঁত মুবারক শহীদ হবার স্থানটিকে গুম্বুজওয়ালা ঘর হিসেবে সংরক্ষিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানকার হযরত আমির হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু’র মাযারকেও গম্বুজ ও লোহার গ্রীলওয়ালা মাযার ঘর বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এরূপ অসংখ্য মাযারের অবকাঠামোগত বর্ণনা করেছেন, যা এরপরই ১৯৩২ সনের দিকে ‘সউদী আরব’ প্রতিষ্ঠার সময় ধ্বংস করা হয়েছে। উহুদের শহীদের মাযার-মসজিদের ছবি মক্কা শরীফ থেকে প্রকাশিত ওই বইটিতেও দেখেছি। শুধু তাই নয়, এয়ার মুহাম্মদ সাহেব প্রণীত সফরনামায় দেখা যায়, মক্কা শরীফে খানায়ে কা’বার সাথে জবলে আবী ক্বোবাইস পাহাড়ের পাদদেশে ‘হযরত গাউসুল আ’যম আবদুল ক্বাদের জীলানী মসজিদ’ ছিল যেখানে তিনি নামায আদায় করেছেন ১৯১৪ সনে। যার অস্তিত্ব বর্তমানে কল্পনাতীত। এরূপ অসংখ্য মসজিদ ও মাযার ভাঙ্গা হয়েছে শুধুমাত্র শির্ক-বিদ‘আত ও হারাম থেকে মানুষকে রক্ষার মিথ্যা অজুহাতে। [সূত্র. মৌলভী হাজি এয়ার মোহাম্মদ কর্তৃক ২৫ মাঘ ১৩৩০ বাংলা সনে প্রথম সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘সফরনামা আরব ও হেজায’র ১১ মার্চ ২০০২ তারিখে কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস, চট্টগ্রাম হতে সাংবাদিক ওবায়দুল হক প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ সংখ্যা]
মোটকথা, সামগ্রিক কর্মকান্ডে এরা সুন্নিয়তের ধারা থেকে আলাদা হয়ে খারেজীদের কট্টরপন্থাকে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে ও এদের পেট্রোডলারের সুফলভোগি ওহাবী-খারেজীরা এখানকার সূফীতাত্ত্বিক উদার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বহুমুখী আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে। মিলাদ মাহফিলে দাঁড়িয়ে (ক্বিয়াম) ‘এয়া নবী সালাম আলায়কা’ পড়ার মতো একটি ভাবগম্ভীর ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এরা একই সাথে মুখ, কলম এবং অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সুন্নিদের বিরুদ্ধে। সবাই মিলে উচ্চস্বরে দুরূদ পড়ার মতো ইবাদতেও এরা বাধা দিচ্ছে। এসব বিষয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা আজিজুল হক শেরে বাংলা রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি সম্মুখবিতর্কে এদের পরাভূত করেছে বহুবার এবং ইসলামী সংস্কৃতির দুশমন হিসেবে চিহ্ণিত করেছে। এখন এদের সমাজ ও সুন্নিদের চেয়ে অনেকটা আলাদা বলা যায়। এদের মাদরাসাগুলো সরকারি মাদরাসা বোর্ড, সরকারি সিলেবাস এমনকি সরকারি কোন বিধি-বিধান পর্যন্ত অনুসরণ করেনা। এখন খারেজ-কওমী মাদরাসাগুলোর টাকা যেমন সউদী আরব থেকে আসে, তেমনি সিলেবাসসহ অন্যান্য অনেক উপাদানও সেখান থেকে পায়। সুন্নীদের সাথে কোন কোন জায়গায় এদের বাড়ি-ঘর, মসজিদ পর্যন্ত পৃথক। ফলে ওহাবী-সুন্নীতে সাংস্কৃতিক পার্থক্যও অনিবার্য হয়ে ওঠে।
মওদুদীপন্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক পার্থক্য শুধু সুন্নিদের সাথে নয় ওহাবীদের সাথেও রয়েছে। ওহাবীরাও বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে আবুল আ‘লা মওদুদী এবং তাঁর অনেক প্রকাশনাকে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেছেন। মওদুদীপন্থীরা মাদরাসা, মসজিদসহ অন্য অনেক ক্ষেত্রে সুন্নি-ওহাবী উভয়ের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকলেও আক্বিদাগত ক্ষেত্রে এরা উভয়ের কাছে বিভ্রান্তিকর। শিয়াদের মতো এরাও ‘সাহাবা-এ কেরাম সত্যের মাপকাটি নয়’ মন্তব্য প্রকাশ করেছে বিভিন্ন বই-পুস্তকে। তাই তাদেরকে সাহাবীদের অনুসারী ধরা যাবেনা বিধায় পূর্বোক্ত হাদীস শরীফ অনুসারে বাতিলদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন অনেকেই।
তাসাউফ বা সূফী দর্শন ইসলামি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। বিশেষত: ভারত উপমহাদেশে এ বাংলাদেশের মানুষ হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হয়েছে সূফী দরবেশদের হাতে; অথচ সেই সব পীর-ফকিরদের বিরুদ্ধে মওদুদীপন্থীদের অবস্থান। মওদুদী সাহেব ‘ডায়াবেটিক রোগিকে যেভাবে চিনি থেকে, সেভাবে মুসলমানদেরকে পীর থেকে দূরে থাকার’ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন নামক বইয়ে ফাতেহাখানি, যেয়ারত, নযর-নেয়ায, ওরস ইত্যাদিকে মুশরিকদের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন, যা সুন্নি মুসলমানরা অন্তত: হাজার-হাজার বছর ধরে পালন করে আসছে। আর যেয়ারত ও ফাতেহা সুন্নাত হিসেবে হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়। সুতরাং মওদুদীর এ জাতীয় উক্তিগুলোর ইসলামি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘাষণার নামান্তর। এরাও ওহাবীদের মতো মাযার-ওরস উচ্ছেদের পক্ষে এবং শিয়াদের মতো সাহাবীদের এমনকি নবীগণ সম্বন্ধে পর্যন্ত বিভ্রান্তিকর আক্বিদার প্রচারক। এ ধরনের ৭২ দলীয় ইসলাম বিকৃতিকারী সম্প্রদায়ের কারণে ইসলামের মূল ধারার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নানাভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। এতদসত্ত্বেও ইসলামের সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির পেছনে আউলিয়ায়ে কেরাম তথা সুফী ত্বরিকার রয়েছে বিশাল অবদান। এরা ক্বোরআন-সুন্নাহ্, ইজমাহ, ক্বিয়াস’র আলোকে নিজ নিজ ত্বরিকার মধ্যে নিত্য নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিয়ে চলেছেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। নবীগণের আগমন বন্ধ হলেও মানুষ যাতে একতরফাভাবে শয়তানের অনুগত হয়ে না যায় এজন্যই নবীর উত্তরসূরী ও খলিফা হিসেবে আউলিয়া ও সংস্কারক ইমামগণ শয়তানী অপসংস্কৃতির প্রতিরোধ করে যাচ্ছেন। তাঁরা ইসলামের প্রচারক, সংস্কারক ও বাতিলের প্রতিরোধকারী হিসেবে দুনিয়ার বুকে সর্বাবস্থায় বিরাজ করেন। ক্বোরআন-হাদীসে আউলিয়া-এ কেরামের যোগ্যতা, মর্যাদা, দক্ষতা ও কর্মময় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে একই সাথে সাড়ে তিন শত আউলিয়ার একটি আধ্যাত্মিক শাসন-প্রশাসন থাকার কথা হাদীস শরীফেই রয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুসারে, শুধু শাম দেশেই চল্লিশ জন আবদাল সব সময় বিরাজ করবেন। এভাবে গাউস, কুতুব, আবদাল, আওতাদসহ বিভিন্ন স্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের সমন্বয়েই আল্লাহর খেলাফত-আউলিয়া সরকারের অধীনে চলতে থাকবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত।
আর এ প্রশাসন হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মাওলা আলী শেরে খোদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক যোগাযোগ রক্ষা করেন। বর্তমানে দুনিয়া ব্যাপী যে কয়েকটি ত্বরিকা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বেগবান করেছে সেগুলো ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্সবন্দিয়া, সুহরাওয়ার্দিয়া নামে অধিক পরিচিত। গাউসুল আযম হযরত আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু দ্বীনকে পুনর্জীবনদাতা ‘মুহীউদ্দীন’ হিসেবে যেমন পরিচিত, তেমনি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ত্বরীক্বা ‘সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরিয়া’রও প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অনুসারী ত্বরিকতপন্থীদের ‘ক্বাদেরী’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও রয়েছে এ ত্বরিক্বার লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরীদ।
বিশেষত: পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ‘দরবারে আলীয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোট’ থেকে আগত গাউসে যামান আল্লামা সৈয়দ আহমদ শাহ্ পেশোয়ারী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এবং গাউসে যামান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে আজ এ ত্বরিক্বার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁদের মাধ্যমে আজ থেকে নয়শত বচর আগে ইরাকের বাগদাদে উদ্ভূত এ ত্বরিক্বার যাবতীয় সংস্কৃতি যেমন, যিকির-দরূদ, খতমে গাউসিয়া শরীফ, গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি আমাদের ঘরে ঘরে অনুসৃত হচ্ছে। এ শতাব্দির সংস্কারক অলি, আল্লামা তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি প্রবর্তিত ‘জশনে জুলূসে ঈদ-এ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’ তথা মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আজ বাংলাদেশে গণ ইসলামি সংস্কৃতির অংশ হয়েছে। সউদী আরবে ওহাবীদের সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক অনুষ্ঠান তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আযানের পূর্বে দুরূদ-সালাম এগুলোর মধ্যে অন্যতম। চৌদ্দশ’ হিজরীর মুজাদ্দিদ আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হির রচিত না’ত-ই রসূল ‘সবসে আওলা ওয়া আ’লা হামারা নবী’ এবং সালাত-সালাম ‘মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম’ আজ চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য এনেছে।
ঠিক সেভাবে চিশতিয়া ত্বরিকার নিজস্ব অন্যান্য কর্মকান্ডের সাথে সাথে ইসলামি গযলের সংযোজন ভারত উপমহাদেশের ইসলামি সংস্কৃতির সাথে এক বিশেষ সংযোজন। মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত শেখ আহমদ ফারূক্বী সিরহিন্দী রহমাতুল্লাহি আলায়হির ইসলামি সংস্কৃতির প্রাচীনতম উপাদান গরু জবাই-গরু কোরবানী বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে এবং স¤্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের দরবারের অনৈসলামিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে কারাগারে গিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা গরু কোরবানি করতে সক্ষম হচ্ছি। এ ভারত বর্ষে ইংরেজ আমলে ও হিন্দু-ওহাবীদের যৌথ উদ্যোগে গরু জবাই নিষিদ্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই সময় আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি তাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নামে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীকে ওহাবীরা দিল্লী শাহী জামে মসজিদের মিম্বরে বসিয়ে বক্তৃতা শুনেছিল, যা এদেশে একটি অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতো। আ’লা হযরত তাদের এ নীতিরও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। বিশেষত: বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সংস্কৃতির সাথে ক্বাদেরিয়া, চিশতিয়া, নক্বশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া ত্বরিকার সমন্বিত সূফী দর্শনের উদ্ভব হয়েছে।
এভাবে সূফীগণের হাতে ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্র দিন দিন প্রসার লাভ করে বিশ্ব সংস্কৃতিকেই তাকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত সূফীগণের এ ধারা অব্যাহত থাকবে। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা নির্মাণে উপরোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ববহ বিবেচনা করতে হবে- অন্যথায় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সংস্কৃতি আশা করা যায়না। বিশেষ করে যে উপাদানাটি ইসলামী সংস্কৃতিতে সে রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের যামানা থেকে গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়ে আসছে তা হলো পূর্বতন সমাজের আচার-আচরণ ও ঐতিহ্য। মনে রাখতে হবে ইসলাম কখনো স্থানীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেনি। কোন স্থানীয় কালচার অমানবিক ও ক্ষতিকর প্রমাণিত না হলে তা কখনো উচ্ছেদ করা হয়নি। ক্বোরআন করীমে পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে; অথচ ইঞ্জীলের বিকৃত সংস্করণ বাইবেলে অনেক নবীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর অভিযোগ আনা হয়েছে, যা ধর্ম গ্রন্থের বিকৃতিরই সাক্ষী বহন করে। কিন্তু ইসলাম পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা প্রমাণ করেছে এবং তাঁদের সময়ের অনেক বিধানকেও বহাল রেখেছে।
ইসলামে এসে ওই বিধানাবলী ও ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা লাভ করেছে। তৎকালীন আরবে যে সব অপসংস্কৃতি সৃষ্টি হয়েছে ইসলাম সেসব উচ্ছেদ করেছে মানবতার কল্যাণের প্রয়োজনে। ইসলাম শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া বন্ধ করেছে। বিধবা বিবাহ্কে উৎসাহিত করতে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম বিয়েটিই ছিল চল্লিশ বছর বয়স্কা হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহার সঙ্গে। আগে পিতা-স্বামী বা ভাইয়ের সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার ছিলনা; অথচ ইসলাম তা দিয়েছে। নারীকে ‘শয়তানের ফাঁদ’ বলা হতো, পাশ্চাত্য প্রাচ্য সর্বত্র। তাকে আল্লাহর ইবাদত করার অধিকারও দেওয়া হতোনা; অথচ ইসলাম ধর্ম পালনে নারী-পুরুষে কোন পার্থক্য করেনি। আগে নারীদের শিক্ষার অধিকার ছিলনা। ইসলাম ‘জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরয’ ঘোষণা করেছে। [আল-হাদীস]
ইসলাম ইতোপূর্বের দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছে। সাদা-কালো-ধনী-গরিবের পার্থক্য দূর করেছে। মানুষের নিজের এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর বিধায় মদ, জুয়া, ব্যভিচারের মতো অপসংস্কৃতি কঠোর হস্তে দমন করেছে। এভাবে ইসলাম যখন যেখানে গেছে স্থানীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও অপসংস্কৃতি উচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করেছে। মুসলমানরা মিশর বিজয়ের পর সেখানকার প্রচলিত অনেক সংস্কৃতি সংরক্ষণ করলেও নীল নদের পানি প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য যুবতী সুন্দরী কন্যা বলি দেওয়ার মতো জঘন্য অপসংস্কৃতি উচ্ছেদ করেছে। ভারতবর্ষে মুসলমানরা প্রায় হাজার বছর ধরে শাসন করেছে, অথচ কোথাও স্থানীয় সংস্কৃতি উচ্ছেদ করা হয়নি। কোথাও মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ নির্মিত হয়নি। কাউকে মুসলমান হতে বাধ্য করা হয়নি। এখনো সমগ্র ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ট, যা মুসলমানদের উদারতার বড় প্রমাণ। পৃথিবীর কোথাও অন্য ধর্মের শাসনে ভিন্নধর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কল্পনাতীত। মুসলমানরা ভারতে নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে সত্য, স্থানীয় সংস্কৃতিকে উচ্ছেদ করেনি। ভারত বর্ষে সেন শাসকরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবন্থান নিয়েছিল, অথচ ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সেনের সাক্ষ্য হলো ‘আমার বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গ ভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।’ স্থানীয় সংস্কৃতির প্রতি ইসলামের মনোভাবের সুফল সম্পর্কে রাহু সাংকৃত্যায়ন তাঁর ‘ইসলাম কী রূপরেখা’য় বলেন, ‘ঔদার্যের কারণে স্থানিকতাকে অস্বীকার করে নেওয়ার ফলেই ইসলাম ভূমন্ডলে সম্প্রসারিত হয়েছে।’ বাস্তবেই এ ঐদার্য্য যখন বিঘিœত হয়েছে তখনই দেখা গেছে বিপত্তি। পাকিস্তান ইসলামের এ বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার পরিণতি হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে, পরবর্তী সময়ে। ততদিনে পাকিস্তান হারিয়েছে তার একটি অংশ এবং ওই অংশের ভাইদের আগের সহানুভুতিও। পাকিস্তানের অনেক সুকীর্তি পর্যন্ত আজ আলোচনায় আনবার সাহস নাই কারো। কারণ, এদেশের পরবর্তী সাংস্কৃতিক অঙ্গন অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তাদের অপমান করে বিদায় করেছে এ দেশ থেকে। পৃথিবীর কোথাও যাতে মুসলমানদের পরিণতি এমন না হয়, যাতে ইসলাম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে শাসন করতে পারে, এজন্যই স্থানীয়তাকে গ্রহণের নযীর স্থাপন করে গেছেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ। আমরা তাঁদেরই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারী। তাই, ইসলামি সংস্কৃতি হঠাৎ আসমান থেকে নেমে আসা কোন কিছু নয়। এটি সমগ্র বিশ্ব সংস্কৃতির পরিচ্ছন্ন একটি রূপমাত্র। ‘সারা বিশ্বে সংস্কৃতির একটি ঐক্যতো আছেই, যার মূলে মানবজাতির ঐক্য, সেই আদি এক পুরুষ ও এক নারীর ঐক্য। কিন্তু আবার অজ¯্র জাতিগত বিচিত্রতায় প্রত্যেকে একটু একটু করে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।’ … ‘ইসলামী সংস্কৃতির যেমন একটি অভিন্ন মৌলিক পাটাতন আছে, তেমনি আছে দেশ ভেদে ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্নতাও।’ [আবদুল মান্নান সৈয়দ, বাংলা সাাহিত্যে মুসলমান পৃ.৪৩,৩]
আবদুল মান্নান সৈয়দ বাঙ্গালী মুসলমানের সংস্কৃতির রূপরেখা তুলে ধরে বলেন, কালচারের দু’টি অংশঃ একটি আদর্শিক; অপরটি স্থানিক। সংস্কৃতির স্থানিকতা ততোক্ষণ গ্রাহ্য যতোক্ষণ আদর্শকে আঘাত করে না। যেমন, বাঙালি মুসলমান স্থানিক পোশাক গ্রহণ করেছে, কিন্তু প্রতিমা পূজা করেনা।’ [প্রাগুক্ত, পৃ.৫১] সুতরাং বাংলাদেশের ইসলামি সংস্কৃতি ও স্থানীয় পরিচ্ছন্ন ঐতিহ্যকে ধারণ করে এবং আদর্শ বিরোধী অংশকে বর্জন করে এগিয়ে চলবে। ইসলামি সংস্কৃতিতে আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ বিনোদনের ও শিল্প সাহিত্য চর্চার পথ অবারিত রাখতে হবে যাতে এসব বিষয়ে কেউ নিজস্ব মাধ্যমের অনুপস্থিতিতে অপসংস্কৃতির ক্রীড়নক হয়ে না যায়। ভালো কবি ও কবিতাকে পৃষ্ঠপোষকতা না দিলে খারাপ কবিদের দৌরাত্ম্য বাড়বে। ইসলাম বিভ্রান্ত কবিদের যেমন নিন্দা করেছে তেমনি উত্তম কবিতার প্রশংসাও করেছে। পবিত্র ক্বোরআনের সূরা ‘আশ-শোয়ারা’য় বলা হয়েছে, ‘‘এবং কবিদের সম্বন্ধে বলা যায়, বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখতে পাওনা। তারা উপত্যকায় উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়, তদুপরি তারা মুখে যা বলে কাজে তা করেনা। তবে যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে অতিমাত্রায় তৎপর রয়েছে এবং অত্যাচারিত হলে নিজেদের আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও কথা প্রয়োজ্য নয়। জুলুমবাজরা সত্বরই জানতে পারবে তাদেরকে কি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।” এ আয়াতের পূর্ব ভাগে ভ্রান্ত কবিদের নিন্দাবাদ এবং শেষভাগে হযরত হাস্সান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু’র মতো কবিদের উৎসাহিত করা হয়েছে; বরং কাফিরদের কবিতার জওয়াবে কবিতা রচনার জন্য উৎসাহিত করে হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ‘যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহও রসূলের সাহায্য করেছে, কথা (কবিতা) দ্বারা আল্লাহর সাহায্য করতে কে তাদের বাঁধা দিয়েছে? [আল হাদীস] উক্ত ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি বর্তমান বিশ্ব এবং আমাদের দেশে সমভাবে প্রযোজ্য। আজ কবিতা এবং সংগীতের নামে চলমান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে ঈমানদার-মুত্তাক্বীদের একই অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসা সময়ের দাবী।
সংস্কৃতির এমন কোনো বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ছিলনা। খ্রিস্টান দুনিয়া যখন অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত তখন ইসলাম জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে আলোকিত করেছে। গবেষণা ও মুক্ত চিন্তার বন্ধ দরজাকে মুক্ত করেছে। মক্কা-মদীনা, কুফা-বসরা, দামেস্ক থেকে স্পেন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের পর গ্রন্থাগার বানিয়েছে। বানিয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ইতিহাস বলুন আর দর্শন বলুন কিংবা অনুবাদ শিল্প বলুন সবকিছুই তো মুসলমানদের অবদান। প্রাচীন বিজ্ঞানের শুরু থেকে সফলতার শীর্ষে আরোহণ পর্যন্ত সবকিছু মুসলমানদের হাতেই হয়েছে যখন ইহুদী-খ্রিস্টানরা নতুন আবিস্কার বা বক্তব্য সহ্য করছিলনা। বিজ্ঞানীদের জীবন্ত কবর দিচ্ছিল। তখন শব্দ বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যার মতো প্রাচীন বিজ্ঞানের এক একটি অধ্যায় আবিস্কার করে যাচ্ছে মুসলমানরা। সাহিত্যিক অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদানের স্বীকৃতি কে না জানে। দর্শন শাস্ত্রে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল শীর্ষ স্থানীয়। ভূগোল, মানচিত্র বিদ্যায়ও মুসলমানদের অবদান ছিল ঈর্ষণীয় পর্যায়ে।
সার্টন (Sarton) তাঁর Indtroduction to the History of Science গ্রন্থে বলেন, ‘‘মানব সমাজের প্রধান কাজ মুসলমানগণ সাধন করিয়াছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল ফারাবী ছিলেন মুসলমান, সর্বশ্রেষ্ঠ গণিত বেত্তা আবু কাবিল ও ইব্রাহিম ইবনে সিনান ছিলেন মুসলমান, সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ও বিশ্বকোষ প্রণেতা আল মাসূদী ছিলন মুসলমান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আততাবারীও ছিলেন মুসলমান।’’ [P.K. Hitti, History of the Arabs সূত্রে, কে. আলী মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস, পৃ.-৩২১]
আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও ইউরোপের যে অগ্রগতি তার ভিত্তি মুসলমানদের হাতে একথা অকপটে স্বীকৃত হয়েছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়- যা মুসলমানদের উন্নত সাংস্কৃতিক ভিত্তির পরিচায়ক। সংস্কৃতির মূল পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র (রাজনীতি) এবং এর চালিকা শক্তি অর্থনীতি-ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ছিল একাধারে হাজার বছরেরও বেশি। সংস্কৃতির উক্ত সব বাহন ছাড়াও বিনোদন শিল্পপটিও এক নতুনত্ব লাভ করেছিল মুসলমানদের হাতে। সংগীত শিল্পটি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলমানদের হাতে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। অশ্লীল যৌন আবেদনময়ী এ শিল্পটিকে মুসলমানরাই পরিচ্ছন্ন বিনোদনের উপযুক্ত করেছে। ‘খলিফা হারুনুর রশীদের দরবারে আয়োজিত এক সংগীত অনুষ্ঠানে দুই হাজার গায়ক অংশ গ্রহণ করেছিলো।’ [কে. আলী. প্রাগুক্ত. পৃ. ২৫৮]
ইমাম গাযালী তাঁর ‘এহইয়া-উল উলুম’ গ্রন্থে নিষিদ্ধ ও বিধিসম্মত সংগীতের বিবরণ দিয়েছিলেন। খ্রিস্টান বিশ্বের নিষিদ্ধ সংগীতের মুকাবেলায় মুসলমানরা বিধিসম্মত রুচিশীল সংগীতের চর্চা করতেন। গাযালী, সংগীতকে ¯œায়ু ও মস্তিস্কের খোরাক বলে মন্তব্য করেন। আবুল ফারাজ ইস্পাহানী আরবীতে সঙ্গীতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করেন, যা ২১ খন্ডে বিনস্থ ছিল এবং এতে একশত প্রকারের স্বরলিপির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ ছিল। বাগদাদে অসংখ্য সংগীত স্কুল ছিল এবং এ সময় সংগীত বিষয়ক বহু গ্রীক গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। আমাদের এ ভারত বর্ষে সংগীত শিল্পের উন্নয়নের জন্য হযরত মাহবূবে এলাহি নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলায়হির খলিফা তুতিয়ে হিন্দু নামে পরিচিত হযরত আমির খুসরু রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি এখনো বিখ্যাত হয়ে আছেন। আমির খুসরু রহমাতুল্লাহি আলায়হি বেশ কিছু বিশেষ বাদ্যযন্ত্র আবিস্কারসহ উচ্চাঙ্গ সংগীতের জন্য বিখ্যাত ব্যক্তি; অথচ আজ এ মাধ্যমটির অপব্যবহার। এ ব্যাপারে উদাসীনতায় হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় অশ্লীলতায় নিমজ্জিত হয়েছে। হস্তলিপি শিল্প (Calligraphy) তখনো মুসলমানদের হাতে ছিল। ইনশাআল্লাহ, এখনো অন্তত, আরবী ক্যালিগ্রাফীতে মুসলমানদের প্রতিভা বিশ্ববরণীয় হয়েছে।
সুতরাং যে সব বিভাগে ইতোপূর্বে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল সে সব মাধ্যমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে যে সব নতুন নতুন দিক বিনোদন ও শিল্পের নামে বাজারে আসছে তাতেও অবস্থান মজবুত করতে হবে। অন্যথায় সে সব মাধ্যম থেকে বিনা প্রতিরোধে ইহুদী-খ্রিস্টান ও আর্য সংস্কৃতির মিসাইল এসে আমাদের সমাজকে লন্ডভন্ড করে দেবে। বর্তমানে দিচ্ছেও। বর্তমানে মেলা’র যে কদর বেড়েছে একে স্বচ্ছ ও সুন্দররূপে কাজে না লাগিয়ে উপায় নেই। জশনে জুলূস এ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হিজরি নববর্ষ, ঈদ উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষে সুস্থ বিনোদনমূলক নতুন নতুন উপাদান যোগ করে মেলার আয়োজন করা দরকার। বই, ক্যাসেট, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও দেশীয় শিল্প সামগ্রির সমাহার করে এ মেলাকে জনপ্রিয় করতে হবে। ফ্যাশন শো-বিজ্ঞাপন শিল্পকেও আমাদের আদর্শ ও বিশ্বাসের আলোকে সাজাতে হবে। অন্যথায়, যেভাবে এই দুই শিল্প পাশ্চাত্যের বেহায়া সংস্কৃতির দিকে এগুচ্ছে শীঘ্রই নতুন প্রজন্মকে মূল্যবোধ বিস্মৃত করে দেবে।
মনে রাখতে হবে, ইসলামে সব নতুন আবিস্কার (বিদ‘আত) নিন্দনীয় নয়। বিদ‘আত-এ হাসানা-ভালো উদ্ভাবন এবং বিদ‘আত-এ সাইয়্যি বা মন্দ উদ্ভাবন এ দুই প্রকার রয়েছে। বিদআত-এ হাসানাহ্ নতুন সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার দলিল হিসেবে যথেষ্ট। ইসলামি সংস্কৃতির পরিসর বাড়াতে ব্যর্থ হলে নতুন প্রজন্ম বিজাতীয় সংস্কৃতিতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য। নিজের ঘর টিকিয়ে রাখতে যুগোপযোগি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ ইসলামই খোলা রেখেছে, ইজমা’, ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের অনুমতি দিয়ে।
বর্তমানে বিয়ে শাদীকে উপলক্ষে করে সঙ্গীতানুষ্ঠান করা হয়। পূর্ববর্তী সময় মুসলিম সমাজে বিবাহের পূর্বরাতে দক্ষ আলিম দ্বারা ওয়াজ-নসিহতের আয়োজন করা হতো। ওই মাহফিলে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য, মাতাপিতার প্রতি নব দম্পত্তির কর্তব্য এবং স্বামীর পরিবার গঠন ও সন্তান-পালনের ইসলাম সম্মত সুন্দর পদ্ধতিগুলো আলোচনা ও রপ্ত করা হতো। এখন ক্রমশ মুসলিম সমাজে এ সুন্নাতটি পালনের ক্ষেত্রে অইসলামী সংস্কৃতি চালু হতে যাচ্ছে। মুসলমানদের বিবাহে বিধর্মীদের সমাজে প্রচলিত অশ্লীল গান-বাদ্য, তাও বিকট ও শব্দ দূষণ সম্বলিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার চলছে দেদারসে। এতে মুসলিম সমাজে ধর্মহীনতা, অশ্লীলতার অনুপ্রবেশ তো ঘটছেই। পক্ষান্তরে আর্থিকভাবেও মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
পরিশেষে, আমি সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত ও সংস্কৃতির অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে লেখার ইতি টানলাম।

